না-লেখা নীল চিঠি
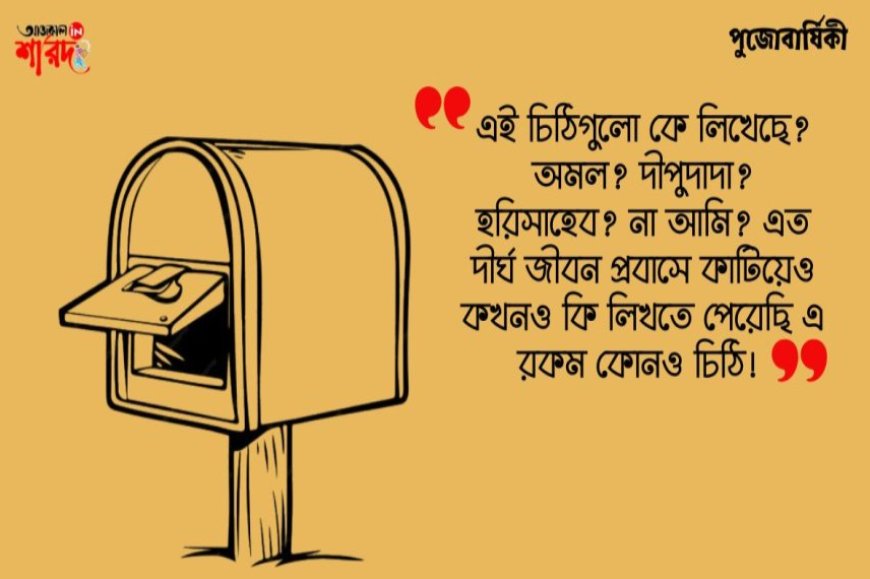
শ্যামলী আচার্য
বাড়িটা ছিল হ্যারি সাহেবের। আমরা বলতাম হরি সাহেব। খেলার মাঠ থেকে এক ঝলক দেখতে পেতাম হরিসাহেব হেঁটে যাচ্ছে কাঁচা রাস্তায়। সাইকেল ঠেলে ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছে। সাইকেলের চাকায় হাওয়া নেই, টায়ার পাংচার। ওর সাইকেলে, ওর বাড়িতে, ওর জীবনে কিছু না কিছু ঝামেলা লেগে থাকত। আমরা হরিসাহেবকে দেখতে পেলেই কেউ একজন হাঁক পাড়তাম বলো হরি। বাকিরা তক্ষুনি সমস্বরে হরি বোল। হরিসাহেব হাসতে হাসতে তাকাত। আমাদের দিকে একটা হাত তুলে সে-ও বলত, হরি বোল। বুঝে বলত, কিংবা না-বুঝে। সেটা বোঝার বয়স হয়নি আমাদের তখনও। মহাপুরুষের বরাভয়-মূর্তির মতো দেখাত দূর থেকে।
ওর বাড়িটা ছিল লাল। পোড়া লাল ইটের। তখন বিলিতি সাহেবদের বাড়িঘরগুলো যেমন হোত। একটু আভিজাত্য, খানিকটা গাম্ভীর্য মেলানো। বাড়িটা দোতলা। নিচে ডাকঘর। লেখা আছে জামনগর পোস্ট অফিস। যাকে আমরা পোস্টাপিস বলতাম। সেকালে প্যান্টের বোতাম-ছেঁড়া কচি ছেলেপুলেদের ‘ওই যে তোর পোস্টাপিস খোলা’ বলে অপ্রস্তুত করা যেত। সেটা তেমনই এক খোলামেলা সময়।
তখন জামনগর পোস্টাপিসে চিঠি আসত। পোস্টমাস্টার যামিনীবাবু আর তার একমাত্র পিয়ন নকুল। আমাদের সে অঞ্চলে সকলের বাড়িঘর চিনত নকুল। কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে চিঠি বের করে কার হাতে দিলে সে চিঠি যথাসময়ে প্রাপকের হাতে পৌঁছবে, নকুলের নখদর্পণে। দুপুরের দিকে কার ঘরে গেলে বিধবা মানুষটা ফলমূল হাতে ধরাবেন, বেলা গড়ালে কোন খুড়িমা জলের সঙ্গে দুটো বাতাসা দেয়, ভরদুপুরের কাঠফাটা রোডে কোন কিশোরী কাঁসার গেলাসে কাগজিলেবু কচলে চিনি মিশিয়ে সঙ্গে দুটো-চারটে নাড়ু ধরায়, সব নকুল জানে। সেরকম আগুপিছু ভেবেই নকুল চিঠি নিয়ে বেরোত।
হরিসাহেবের বাড়ির দোতলায় একটি বড়সড় ঝুল-বারান্দা। বারান্দায় হরিসাহেবের মা বসে থাকত। একটা ইজিচেয়ার। অমন চেয়ার শান্টুদের বাড়িতেও দেখছি। শান্টুর জ্যাঠা সেখানে বসে হুঁকো খায়। হরিসাহেবের মা অবিশ্যি হুঁকো খেত না, চা খেত। সাদা কেটলি থেকে ঢেলে সুড়ুত সুড়ুত করে। ও, হ্যাঁ, ঐ কেটলিকে টি-পট বলে, সেটা আমি বড় হয়ে জেনেছি। কেটলিতে একটা জামা পরানো থাকত, আরও পরে বিদেশে গিয়ে জেনেছি ওকে বলে টি-কোজি। বারান্দায় যে ফুললতা বেয়ে উঠেছিল চুপচাপ, তার নাম ব্লিডিং হার্ট। সে নামটিও জানা ছিল না। রক্তমাখা ফুল দেখে অবাক হতাম, ভয় পেয়েছি। কিন্তু সে লতা যখন আমার বিলিতি বারান্দার সুদৃশ্য টবে ঝলমল করে উঠল, আমার ছেলেবেলার ফেলে-আসা সময়টি কাঁটার মতো বিঁধে গেল চোখে। চোখ থেকে জল নয়, রক্ত পড়েছিল ফোঁটা ফোঁটা। মনের মধ্যে রিনরিন করে বাজছিল কচি সুর। বলো হরি। হরি বোল।
হরিসাহেবের বাড়ির একটু দূরেই নদী। চণ্ডীমণ্ডপের জ্যাঠা-দাদা-খুড়োরা বলে, এই নদীর পাড়ে স্টিমার থেকে একদিন হরিসাহেব আর তার মা নেমেছিল। এর পর কেউ আর কোনও দিন স্টিমারের ‘ভোঁ’ শোনেনি। নদীর জল আর স্টিমারের ভার বইতে পারে না। হাটুরেদের নৌকো এসে মালপত্র নামায়। তারাও আসা-যাওয়া বন্ধ করল একদিন। কী এক সোঁদা গন্ধে ভারী হয়ে উঠত নদীর পাড়। দূরে শ্মশানে ধিক ধিক জ্বলে ওঠা চিতায় পুড়ে যেত বুড়োরা। আমাদের ছেলেবেলার দিনগুলো গোলাপের নরম পাপড়ির মতো একটা একটা করে খসে পড়ত। লাল ডাকবাক্সে চিঠি ফেলত হরিসাহেব, হরিসাহেবের মায়ের লেখা চিঠি। অমল দেখেছে সে চিঠির রঙ নীল। উত্তর আসেনি। এলে নকুল জানত। উত্তর না পেয়েই হরিসাহেবের মা মরে গেল একদিন। বাগানে কামিনীফুল ছাওয়া মাটিতে তাকে গোর দিল। হরিসাহেবও পাশে শুয়ে পড়ল একদিন। আর উঠল না। আমরা আড়চোখে চেয়ে দেখতাম ভরা পূর্ণিমায় হরি সাহেবের বাড়িতে পরীদের আনাগোনা। গায়ে কাঁটা দিত। সেদিন থেকে নদীটাও কী বুড়ো হয়ে গেল?
হরিসাহেবের বাড়িটার ছাদে মাঝে মাঝে চাঁদ ঝুলে থাকত। সেদিন অন্য কোথাও জ্যোৎস্না উঠত না। কেবল এই বাড়িটা ঘিরে থাকত আলো। ঠান্ডা হাওয়া। নদীর পাড় থেকে বয়ে আসা সেই হাওয়ায় হু হু ডাক। লালমুখো ইংরেজ চলে গেলে যে ছেঁড়া ড্রেসিং গাউন ফেলে যায় সেই ফুটোর মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতাম আধখাওয়া চাঁদ। নকুলের বিলি করা চিঠি ডুকরে কেঁদে উঠত কোনও আনাচে-কানাচে। কোন পরবাসে অকালে মরেছে কে, সিঁদুর মুছে শাঁখা ভেঙে ফ্যাকাশে চেহারায় তার শুকনো মুখ ওই চাঁদের আলোয় ভাসে। সেই দিনগুলো বড় নিড়বিড়ে। রসগোল্লা খেয়ে হাত না ধুলে যেমন চ্যাটচেটে আঠা-অসোয়াস্তি লেগে থাকে, তেমনই দুঃখ জেগে থাকত মগজের চিলেকোঠায়।
চাঁদ ঝুলে থাকা দেখে মনে কুডাক। আজ খবর আসবে। অমল বলত, নীল চিঠি আসবে নকুলের হাতে।
যেদিন এই ঘটনা ঘটত, সেদিন আগেভাগে নকুল কাজে বেরিয়ে যেত। কাঁধে নস্যির গন্ধ-মাখা ময়লা ঝোলা। দুপুরের পর থেকে ছোট্ট শহরটা থমথমে। কেন জানি না এইদিনে আমাদের ঠাকুমা সন্ধে হলে থাবড়ে থাবড়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে চাইত। আমরা রূপকথার গল্পের দৈত্যদানোদের পাশে ডেকে ভীতুমনে জেগে থাকতাম। চোখ এঁটে বন্ধ করা, যেন গাবের আঠায় জড়িয়েছে দু-চোখের ঢাকনা। কান সজাগ। পাতা খসে পড়লেও টের পাব।
আমাদের দীপুদাদা একদিন নেই হয়ে গেল। বড় বিলে নেমেছিল। সাঁতার-জানা ছেলেটা সন্ধের পরে স্থির হয়ে ভেসে উঠল। নকুল সেদিন দুপুরেই চিঠি দিয়েছিল হাতে। কীসের চিঠি? রেলের চাকরিতে ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছিল দীপুদাদা। চাকরির বড়কর্তা নাকি জবাব দিয়েছে তাকে। সেই চিঠি? শুনলাম কানাঘুষো। এলোমেলো ছড়িয়ে যাওয়া শিমুলতুলোর মতো ভেসে বেড়াল তার অকালমৃত্যু। তারপর বেশ কবার নতুন করে ফুল ফুটল আমাদের কৃষ্ণচূড়ার ডালে। কয়েকটা শিউলিগাছ ঢলো ঢলো। স্থলপদ্মের গোড়ায় জল জমে নেতিয়ে পড়ল। কয়েকটা পাখি পালক বদলাল। আমরা যখন দীপুদাদাকে ভুলে যাব ভুলে যাব করছি, সেই সময়ই সে ফিরে এল। যেন জঙ্গলে ছিল এতদিন। জঙ্গলে না পচা-পানা ডোবায় বুঝি না। কিন্তু অন্য প্রাণী এক। গায়ে সবুজ গন্ধ। এই নতুন দীপুদাদাকে কোনও কোনও দিদি-বৌদি চুরি করে নাড়ু-তক্তি-নিমকি খাওয়াত। একদিন কমলাপিসি ওর মাথায় চুড়ো বেঁধে দিল। ময়ুরের পালক গুঁজে দিল কে জানি কে। আশ্বিনে ভিক্ষে করতে আসা একচোখ কানা বোষ্টুমী খঞ্জনী বাজিয়ে গান ধরল--
ও কালা তোর তরে আর কতকাল
কদমতলে চেয়ে থাকি।
সেদিন নদী থেকে একটি নতুন হাওয়া উঠল। এরকম হাওয়া এর আগে কখনও আসেনি। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে সারা শহরটি ঘুমিয়ে পড়ল। যে শিয়ালগুলি প্রহর ডাকত, সেদিন তারাও কেন জানি চুপ। গাছের পাতারাও শব্দহীন।
ততদিনে আমরা লায়েক। দিনে-রাতে পরী দেখার নেশা ধরেছে আমাদের। ভয়ডর কেটে গেছে। আলেয়া দেখে চিনতে পারি। নকুলের হাতে চিঠি দেখলে ডাকটিকিট পরখ করি।
হরিসাহেবের বাড়ির পাশে একটি ছোট ডোবা। মজে-যাওয়া। তার পাড়ে একটি বুড়ো বট। ঝুরি নেমে এসেছে মাটিতে। আড়াল করে আছে বুনো কামরাঙাকে।
সে রাত ছিল ঘন অন্ধকার। হঠাৎ বাঁশি বেজে উঠল। কী অপার্থিব সে সুর। অন্ধকারের ভিতর থেকে অন্যরকম আলো আসে। ঘন বটপাতার ফাঁক দিয়ে একটি আধভাঙা চাঁদ হরিসাহেবের বাড়িটার কার্নিশে ঝুলে পড়ল। দোতলার একটি জানালা খুলে গেল। সেখানে দেখা গেল একটি মুখ। ফ্যাকাসে। থরোথরো। মুখটি ফিস ফিস করে ডাকল, হ্যারি, ডার্লিং, চিঠিটা কি এসেছে?
কার চিঠি? কোন চিঠি? আমি অমলের দিকে তাকালাম। অমল ঠাকুর্দার দিকে। পাশে দীপুদাদা ভরা জ্যোৎস্নায় ডোবার ধারে বাঁশিতে বিভোর। এই দীপুদাদাকে আমরা কখনও দেখিনি। কখনও চিনিনি। জানিনি। যেন কোন এক রূপের জগতে তার বাড়ি। সে রূপের জগতের সুর বাজিয়ে চলেছে। এই বাঁশির সুরে হরিসাহেবের বাড়ির উপরে ধীরে ধীরে একখণ্ড মেঘ জমল। ঝির ঝির করে বৃষ্টিও ঝরল। শান্ত হাওয়া বইল। হাস্নুহানার উগ্র গন্ধে ভরে গেল চারিদিক।
এই সময় হরিসাহেবের ঝুল বারান্দার দরজাটা খুলে গেল। একটি মেয়ে ঘোর-লাগা চোখে বারান্দা থেকে হেঁটে হেঁটে নিচে নেমে এল। হাওয়ার মধ্যে পা ফেলে ফেলে মেয়েটি এল পুকুরটির পাড়ে। ভেসে চলেছে যেন। পুকুরের সামনে এসে ধবধবে সাদা ঘাঘরাটা সামান্য একটু উঁচু করে ধরল। তারপর পুকুরের জলের উপর তার কোমল ফর্সা পা রাখল। অমল ফিসফিস করে বলল, নিশি নিশি। দীপুদাদার বাঁশিতে সাপুড়ে-সুর। ছুটকি আমার হাত খামচে ধরল। চেঁচিয়ে বলল, ও দাদা, চোখ বন্ধ কর। চোখ বন্ধ কর।
চোখ বন্ধ করব কি? আমাদের চোখ কি তখন আমাদের চোখের মধ্যে ছিল? চোখগুলো সব বাইরে বেরিয়ে পড়েছে নিজের ইচ্ছেয়। মেয়েটির পিছে পিছে ঘুরছে। ফিরছে। তার গা থেকে ঝরে পড়া আলো প্রাণের মধ্যে টুক টুক করে কুড়োচ্ছে। হিম-সন্ধ্যায় এই চোখহীন অন্ধ চোখ-কুঠুরী থেকেই আমরা দেখতে পেলাম, বড় বিলের মাঝখান অবধি সার-বাঁধা পায়ের ছাপ। সে ছাপ মিলিয়ে যায় না। জেগে থাকে। দূরে কুয়াশা-ঘেরা জলের মাঝখানে ফুটে আছে একটি বিশাল আকৃতির অনন্ত ফুল। কত শত তারা সে ফুলটিকে পাহারা দিচ্ছে। ঝিকমিক জ্বলে তারার আলো। ফুলের পাপড়ি সত্যি সত্যি অনেকগুলো নীল চিঠি। যে চিঠির নকুল নাগাল পাবে না কখনও।
এই চিঠিগুলো কে লিখেছে? অমল? দীপুদাদা? হরিসাহেব? না আমি?
এত দীর্ঘ জীবন প্রবাসে কাটিয়েও কখনও কি লিখতে পেরেছি এ রকম কোনও চিঠি!
.....................................................................................................................
কৃতজ্ঞতা— এই লেখাটির কিছু অংশের জন্য গদ্যকার কুলদা রায়ের একটি ফেসবুক পোস্টের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী।